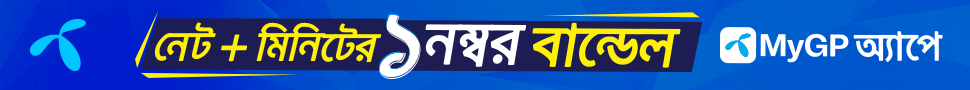ভারত-চীনে মার্কিন শুল্কারোপে বাংলাদেশের পোয়াবারো
- বাংলাকন্ঠ রিপোর্ট:
- প্রকাশ: ১২ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৬ AM , আপডেট: ১২ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৫৬ AM
-11242.jpg)
যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫ শতাংশ শুল্কারোপ বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকদের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে এসেছিল। এরপর দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শুল্ক ২০ শতাংশে নামিয়ে আনে ট্রাম্প প্রশাসন। তবে মার্কিন এই শুল্কারোপের সিলসিলায় বড় ধাক্কা এখন অপ্রত্যাশিতভাবে এক বড় সুযোগে পরিণত হয়েছে। পোশাকের অনেক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বা বায়ার, আগে যারা চীন ও ভারত থেকে পোশাক কিনত—-তারা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে অর্ডার নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু করেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) আরোপ করেন—যা তখনও পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের প্রস্তাবিত হারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল—তখন রপ্তানিকারকরা প্রধান রপ্তানির এখাতে বড় আঘাতের আশঙ্কা করেছিলেন।
তবে নাটকীয়ভাবে, ১ আগস্ট শুল্কারোপের সময়সীমার কয়েক ঘণ্টা আগে—যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর শুল্ক কমিয়ে ২০ শতাংশ করে, এবং ভারতের ক্ষেত্রে তা ২৫ শতাংশ করে বাড়ায়। এছাড়া রাশিয়ার তেল কেনার কারণে ২৭ আগস্ট থেকে ভারতের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্কারোপের ঘোষণা দেয়। এই পরিবর্তন পুরো চিত্রটাই বদলে দিয়েছে।
ভারত, চীন ও মিয়ানমার থেকে আগে যেসব ক্রেতা অর্ডার করত, তারা এখন বাংলাদেশে কার্যাদেশ দিতে প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ করছে। স্থানীয় পোশাক প্রস্তুতকারকরা এই সুযোগটি কাজে লাগাতে আগে স্থগিত রাখা কারখানা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা পুনর্জীবিত করছেন। এছাড়া বন্ধ থাকা কারখানা খোলা এবং নতুন বিনিয়োগের কথাও ভাবছেন।
কেবল দেশীয় প্রতিষ্ঠানই নয়, এর প্রভাব পড়ছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রেও। বৈশ্বিক সোর্সিং প্রবণতা বদলাতে দেখে চীনা বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে নতুন উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন। ট্রাম্পের শুল্ক, যা একসময় হুমকি মনে হয়েছিল—সেটিই এখন দেশের অন্যতম বড় বাণিজ্যিক সুযোগে পরিণত হয়েছে।
স্নোটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম খালেদ বলেন, "আমাদের কারখানায় অর্ডার বেড়েছে, বেশিরভাগই আমেরিকান বায়ারদের কাছ থেকে।" প্রায় ৩০ কোটি ডলারের বার্ষিক রপ্তানিকারক এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার জানান, গত বছর এক মার্কিন বায়ারকে ৩ লাখ ডাউন জ্যাকেট রপ্তানি করেছিলেন, এবার সেই ক্রেতা ৫ লাখ পিস নিতে চাইছেন। অন্য এক ক্রেতা ৬০ হাজার পিস থেকে বাড়িয়ে ১.৫ লাখ পিসের অর্ডারের জন্য আলোচনা শুরু করেছেন।
তিনি আরও জানান, চাহিদা মেটাতে কারখানার সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা চলছে। "নতুন ক্যাপিটাল মেশিনারি (মূলধনী যন্ত্রপাতি) আমদানি করতে হবে। বর্তমানে আমাদের ৩০টি প্রোডাকশন লাইন আছে, যা সম্প্রসারিত হয়ে ৪৫টি হতে পারে।"
অনন্ত গার্মেন্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইনামুল হক খান বাবলু বলেন, "আমাদের ডিসেম্বর পর্যন্ত অর্ডার লাইনআপ হয়ে আছে। সম্প্রতি দুই মার্কিন ক্রেতার প্রতিনিধি প্রাথমিক আলোচনার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু স্পেস এভিলেবল না থাকায় অর্ডার নিতে পারিনি।"
বিজিএমইএর সিনিয়র সহ-সভাপতি বাবলু আরও বলেন, "ক্রেতারা ফ্রি ক্যাপাসিটির (সক্ষমতা) কারখানা খুঁজছেন। কারখানাগুলো সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। আমরাও প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে নতুন ওয়াশিং প্ল্যান্ট নির্মাণ শুরু করেছি।"
তিনি আরও বলেন, "চীন, ভারত ও মিয়ানমারের ওপর আমেরিকান শুল্ক আমাদের চেয়ে বেশি হওয়ায়—সেই অর্ডারগুলো বাংলাদেশে আসবে। বায়রদের কাছে বিকল্প অপশন খুব বেশি নাই। এদিকে ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার সক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা আছে, তাই তারাও দ্রুত উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে পারবে না।"
শুধু পোশাক খাত নয়, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের উদ্যোক্তারাও নতুন বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছেন।
বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল গত ১০ আগস্ট ঢাকার এক অনুষ্ঠানে বলেন, "এখন বিনিয়োগের সেরা সময়।" উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারি সহায়তা চেয়ে তিনি জানান, "আমরা আবার বিনিয়োগে প্রস্তুত।"
২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বিটিএমএ'র উদ্যোক্তারা বস্ত্র খাতে ৩ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন। তবে গ্যাস সংকটসহ নানা কারণে কিছু বিনিয়োগকারী সরে যান। প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণও প্রকাশ করা হয়নি।
মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির তথ্যে তাদের সতর্ক অবস্থানের চিত্র ফুটে ওঠে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২৩–২৪ ও ২০২৪–২৫ অর্থবছরে ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি কমেছে, সর্বশেষ অর্থবছরে তা আগের বছরের তুলনায় ২৫.৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
রাসেল জানান, পোশাক খাতে মোট বিনিয়োগ প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ডলার। তবু গত এক বছরে অনেক বড় গার্মেন্টস গ্রুপ ব্যাপকভাবে সক্ষমতা বাড়িয়েছে, যদিও এসময়ে কিছু বড় কোম্পানিও বাজার ছেড়ে গেছে।
নাম না প্রকাশের শর্তে বিজিএমইএ'র এক নেতা বলেন, হা-মীম গ্রুপ, নিউ এজ গ্রুপ, ডেকো, প্যাসিফিক গ্রুপ ও স্প্যারো গ্রুপ— সবাই সম্প্রতি তাদের সক্ষমতা বাড়িয়েছে। উদ্যোক্তারা মনে করছেন, চাহিদা বাড়ার এ সময়টাই কাজে লাগানোর সেরা সুযোগ।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বায়ার ওয়ালমার্ট, গ্যাপ ইনকসহ ইউরোপীয় ব্র্যান্ড বার্সকার সঙ্গে বাংলাদেশে অর্ডার বাড়ানোর পরিকল্পনা জানতে যোগাযোগ করে টিবিএস। তবে এই প্রকাশের সময় পর্যন্ত তাদের থেকে কোনো সাড়া মেলেনি।
বন্ধ কারখানা পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা
বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, গত দুই বছরে ১৯১টি কারখানা বন্ধ হয়েছে, যার বেশিরভাগই ছোট। একই সময়ে প্রায় ১০০টি নতুন কারখানা উৎপাদন শুরু করেছে। বন্ধ হওয়া কারখানার মধ্যে বড় কারখানায় ১৫ হাজার পর্যন্ত শ্রমিক ছিল।
বিজিএমইএ নেতারা মনে করছেন, বাজার পরিস্থিতি উন্নত হলে – বড় ও ছোট উভয় ধরনের বন্ধ কারখানাই পুনরায় চালু হতে পারে।
ইনামুল হক খান বাবলু বলেন, "ফুল ফোর্সে অর্ডার ফিরে আসায় – বন্ধ কারখানা পুনরায় চালুর সুযোগ তৈরি হবে। আমরা ইতোমধ্যে এগুলো রিভাইভ করা নিয়ে আলোচনা করছি।"
৯ মাস আগে বন্ধ হয়ে যায় ১০০ জন কর্মীর কারখানা গাজীপুরের টঙ্গীতে অবস্থিত জ্যাকস সোয়েটার লিমিটেড। এখন এটি পুনরায় চালুর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, "পৈতৃক জমিজমা বিক্রি করে ব্যবসা পুনরায় চালু করার চেষ্টা করছি।"
ইউরোপে বাড়তি প্রতিযোগিতা নিয়ে শঙ্কা
এই আশাবাদের মাঝেও কেউ কেউ সতর্ক রয়েছেন। তাদের আশঙ্কা, প্রতিযোগী যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজার হারাবে, তারা ইউরোপের বাজার হিস্যার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু করবে। এতে দাম কমে যাবে এবং বাংলাদেশের রপ্তানিকাররা চাপের মুখে পড়বেন।
জাবের অ্যান্ড জুবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক রাশেদ মোশাররফ বলেন, "মার্কিন বাজার সংকুচিত হলে চীন ও ভারতের রপ্তানিকারকরা ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে ইউরোপের দিকে ঝুঁকবে। এতে দাম কমে যাবে, যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর।"
তিনি আরও বলেন, "চীন ও ভারত বর্তমানে যে ধরনের পণ্য তৈরি করছে, সেগুলো তৈরি করতে বাংলাদেশের অন্তত এক বছর সময় লাগবে।"
বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানির অর্ধেকের বেশি যায় ইউরোপে, আর যুক্তরাষ্ট্রে যায় ২০ শতাংশেরও কম।